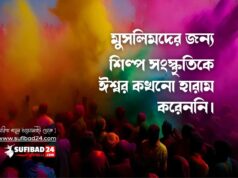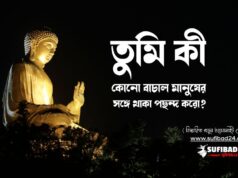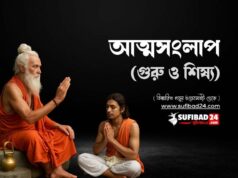দুঃখনিরোধের গভীর দর্শন
দুঃখ জীবনের সহজাত সত্য। এটি কেবল বেদনা বা ক্ষতি নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষণে লুকিয়ে থাকা এক গভীর সত্য। গৌতম বুদ্ধ প্রথম এই দুঃখকে জীবনের এক পবিত্র সত্য (আর্যসত্য) হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তিনি বললেন, “সর্বং দুঃখং”—সবকিছুই দুঃখময়। জন্মে দুঃখ, বার্ধক্যে দুঃখ, রোগে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ দুঃখ, অপ্রিয়ের সান্নিধ্য দুঃখ। যা কিছু ক্ষণস্থায়ী, তা দুঃখের কারণ। জগৎ অনিত্য—প্রতি মুহূর্তে এর রূপ বদলায়, এর স্রোতধারায় মানুষের মন যা ধরে রাখতে চায়, তা হারিয়ে যায়। ফলে, জীবন ভরে ওঠে বেদনা, হতাশা, ও অতৃপ্তিতে।
বুদ্ধ শিক্ষা দিলেন, দুঃখের উৎস বাহ্যিক জগতে নয়, মানুষের মনের গভীরে—তার অবিদ্যা ও বাসনায়। সুখ আছে, কিন্তু তা ক্ষণিক, তরঙ্গের মতো উঠে-নামে। সুখের পশ্চাতে ছুটতে গিয়ে মানুষ বুঝতে পারে না যে, এই সুখই দুঃখের বীজ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন একটি ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাকে ধরে রাখতে চাই, কিন্তু ফুল শুকিয়ে যায়, আর তার শুকিয়ে যাওয়া আমাদের দুঃখ দেয়। মন ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্তি খোঁজে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বাসনাকে মেটায় না, বরং তাকে আরও উত্তপ্ত করে। এই বাসনার আগুনে সমাজে বিবাদ জন্মায়—রাজার সঙ্গে রাজার, শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির, এমনকি মা-পুত্র, ভাই-বোনের মধ্যেও। দার্শনিক প্লেটোর মতো বুদ্ধও বুঝেছিলেন, মানুষের অতৃপ্তি ও বিবাদের মূলে রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা—অসত্যকে সত্য মনে করা।
অবিদ্যাই দুঃখের প্রধান কারণ। অবিদ্যা মানে কেবল জ্ঞানের অভাব নয়, বরং সম্যক জ্ঞানের অভাব—অনিত্যকে নিত্য ভাবা, অসত্যকে সত্য মনে করা। যেমন, উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, “মায়া” বা ভ্রম মানুষকে সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অবিদ্যার কারণে মানুষ এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারকে চিরস্থায়ী মনে করে, আর এই ভ্রম থেকে জন্ম নেয় তার আসক্তি। মনের গভীরে সংস্কার—পূর্বজন্মের কর্ম, সমাজের বিশ্বাস, পরম্পরার ছাপ—এই সব মিলে চেতনা গঠন করে। এই চেতনা থেকে মন, মন থেকে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় থেকে অনুভূতি, অনুভূতি থেকে বাসনা, বাসনা থেকে আসক্তি, আর আসক্তি থেকে ভব—পুনর্জন্মের চক্র। দার্শনিক হেরাক্লিটাসের মতো, যিনি বলেছিলেন “পান্তা রেই” (সবকিছু প্রবাহিত), বুদ্ধও দেখিয়েছেন, জগৎ প্রবাহমান, আর এই প্রবাহে আসক্তি দুঃখের জন্ম দেয়।
এই ভবচক্রের প্রথম কারণ অবিদ্যা, আর এর চূড়ান্ত ফল দুঃখ। কিন্তু বুদ্ধ বললেন, দুঃখনিরোধ সম্ভব। দুঃখের কারণকে রোধ করা যায়। এই নিরোধই জীবনের সর্বোচ্চ সাধনা। অবিদ্যা থেকে মুক্তি মানে সম্যক জ্ঞানের আলোয় প্রবেশ—নির্বাণ। নির্বাণ কোনো স্বর্গীয় লোক নয়, বরং মনের এক অবস্থা, যেখানে বাসনা, আসক্তি, ও অহং লুপ্ত হয়। এটি সেই মুহূর্ত, যখন মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করে, যেমন সুফি দার্শনিক রুমি বলেছিলেন, “নিজের বাইরে নয়, নিজের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করো।”
দুঃখনিরোধের পথে প্রথম ধাপ হলো অবিদ্যাকে চেনা। যখন মানুষ বোঝে যে তার দুঃখের কারণ বাহ্যিক জগতে নয়, তার নিজের মনের ভ্রান্ত ধারণায়, তখন সে মুক্তির পথে পা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মানুষ ধন-সম্পদে সুখ খুঁজতে পারে, কিন্তু যখন সে বোঝে যে সম্পদ অনিত্য, তখন সে সম্পদের পশ্চাতে ছোটে না। বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই মুক্তির পথ দেখায়—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। এই পথ মানুষকে অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে। দার্শনিক কান্টের মতো, যিনি বলেছিলেন, “মানুষের মুক্তি তার নিজের যুক্তি ও সচেতনতায়,” বুদ্ধও দেখিয়েছেন, মুক্তি মানুষের নিজের হাতে।
দুঃখনিরোধ কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন নয়, এটি মনের গভীর রূপান্তর। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে, “আত্মানং বিদ্ধি”—নিজেকে জানো। নিজেকে জানার মাধ্যমে মানুষ বোঝে, দুঃখ তার মনের সৃষ্টি। মন যখন বাসনা, আসক্তি, ও অহং থেকে মুক্ত হয়, তখন দুঃখের কারণও লুপ্ত হয়। এই মুক্তির মুহূর্তই নির্বাণ—যেখানে মন শান্ত, জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত। যেমন সুফি সাধক আল-হাল্লাজ বলেছিলেন, “আনাল হক” (আমিই সত্য), তেমনি নির্বাণে মানুষ নিজেকে সত্যের সঙ্গে একাকার অনুভব করে।
নির্বাণ কোনো দূরের গন্তব্য নয়, এটি এখানে, এখন। প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকা, জগতের অনিত্যতাকে মেনে নেওয়া, বাসনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া—এই পথেই নির্বাণ। যেমন দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন, “সত্যের উপলব্ধি হলো স্বাধীনতা,” তেমনি বুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে সেই স্বাধীনতার পথ দেখায়। এটি কোনো ধর্মের একচেটিয়া নয়, বরং মানবতার সার্বজনীন সম্ভাবনা। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে এই মুক্তির বীজ। বুদ্ধের শিক্ষা সেই বীজকে জাগিয়ে তোলে—অবিদ্যার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয়, দুঃখের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আনন্দে।
নির্বাণ এক নতুন জাগরণ। এক নতুন সূর্যোদয়।
লেখা: ফরহাদ ইবনে রেহান