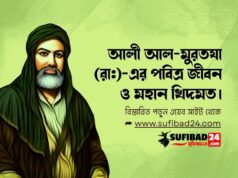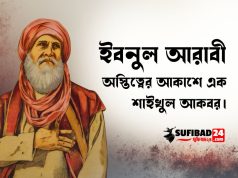কাজী আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.) এর জীবন ও পরিচয়।
উস্তাজুল উলামা কাজী আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.): জ্ঞানের দরবেশ ও আধ্যাত্মিক সাহিত্যসাধক
বাংলার ইতিহাসে এমন কিছু সাধক আছেন, যাঁরা কলমের আলোয় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন, আবার আত্মার তপস্যায় জিকিরের আগুন প্রজ্বলিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.)—চট্টগ্রামের সেই দরবেশ আলেম, যিনি জ্ঞান, সাহিত্য, তাসাউফ ও মানবিক চেতনার মিলনে এক অনন্য মহিমার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক মেধা, যেখানে পাণ্ডিত্য ও প্রেম, যুক্তি ও জিকির, ভাষা ও নূর—সব মিলেমিশে গড়ে তুলেছিল এক আধ্যাত্মিক চিন্তার ভূমি।
জন্ম ও পারিবারিক বংশধারা:
১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কদুরখীল গ্রামে জন্ম নেন, জ্ঞান ও আত্মার সাধক—আল্লামা কাজী আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.)। তাঁর পিতা হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ আলী (রহ.) ছিলেন পণ্ডিত, ধর্মপ্রাণ ও জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব।
জন্ম ও শৈশব:
ইসলামাবাদী (রহ.)—এর জন্ম চট্টগ্রামের কদুরখীল গ্রামে, এক ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে। ছোটবেলাতেই তাঁর মুখে কুরআনের শব্দ ঝরতো যেন শিশিরধারা। গ্রামের মসজিদ, খালপাড়, আর সূর্যাস্তের আলোয় তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হয় তাজবীদ, কিরাত ও ফিকহে। বলা হয়, শৈশবে তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন, তখন তাঁর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে গ্রামের বৃদ্ধরা বলতেন—“এই শিশুর কণ্ঠে নূরের ছোঁয়া আছে।” তাঁর অন্তরে সেই নূরের আলোই পরে সাহিত্যে ও জ্ঞানে এক দীপ্ত ধারার জন্ম দেয়।
শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য:
তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন, যেখানে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও সাহিত্যপণ্ডিতগণ। সেখানে তিনি আরবি ব্যাকরণ, ফারসি সাহিত্য, বালাগাত, ওলুমুল বায়ান এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে ডাকতেন “আলেমে কাব্যপ্রাণ”—কারণ তিনি যুক্তিকে ভালোবাসতেন, কিন্তু আবেগ ও রূহানিয়তের ছোঁয়ায় তাকে জীবন্ত করে তুলতেন। একবার এক শিক্ষক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “ইলমের মূল কী?” তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন— “ইলমের মূল নূর, আর নূরের মূল বিনয়। যে জানে সে কথা কম বলে, কিন্তু হৃদয়ে বহন করে মহাসমুদ্র।”
নিভৃতচারী সুফি ও তাঁর আধ্যাত্মিক আলোকচ্ছটা:
হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন নিভৃতচারী ও গোপনীয়ভাবে মারিফতের রত্নভাণ্ডার সংরক্ষক। তিনি তাসাউফের গুপ্তপথে চলতেন, যেখানে প্রচারের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা সামাজিক মর্যাদার প্রলোভন তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। তাঁর সাধনা ছিল অন্তর্মুখী, নীরব এবং পরিপূর্ণ—যেখানে তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। ইসলামাবাদী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫১ সালে। তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আসে হযরত শাহ সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসি (রহ.)—এর সান্নিধ্য থেকে। ওয়াইসি হযরতের জন্মস্থান চট্টগ্রামের আমিরাবাদে হলেও, তিনি পরবর্তীতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ও স্বল্পকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। মাদ্রাসার পাশেই ছিল তাঁর দরবেশখানা—যেখানে আলেম, ছাত্র ও সাধকরা নিয়মিত উপস্থিত হতেন। ইসলামাবাদী (রহ.)—এর সৌভাগ্য হয়েছিল এই দরবেশখানায় নিয়মিত সান্নিধ্য লাভ করা। ইসলামাবাদী (রহ.) ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর ওয়াইসি হযরতের নিকটে ছিলেন। এই সময় তিনি নীরব সাধনা, রিয়াজত ও মুরাকাবার মধ্য দিয়ে মারিফতের গুপ্তধন লাভ ও সংরক্ষণ করেন। দীর্ঘ সাধনার পর তিনি ওয়াইসি (রহ.)—এর কাছ থেকে তরিকতের খেলাফত গ্রহণ করেন। তাঁর তরিকতের সিলসিলা মুবারক পৌঁছে যায় হযরত ইমাম রাব্বানী শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহ.)—এর মাধ্যমে। ওয়াইসি হযরতের সান্নিধ্য ইসলামাবাদী (রহ.)—এর জীবনের প্রতিটি স্তরে দীক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তায় প্রতিফলিত হয় সেই গুপ্ত আলোকচ্ছটা—যেখানে জ্ঞান ও প্রেম একীভূত, যুক্তি ও অনুভূতি পরস্পরের পরিপূরক। ইলমে দ্বীন, আত্মশুদ্ধি ও সমাজসেবার যে সুমিলন আমরা তাঁর জীবনে দেখি, তা মূলত ওয়াইসি হযরতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও ইসলামাবী (রহ.)—এর নিভৃতচারী সাধনার ফল। সুতরাং বলা যায়—হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসি (রহ.) ছিলেন ইসলামাবাদী (রহ.)—এর আধ্যাত্মিক জীবনের এক অনন্য মাইলফলক। তাঁর পাঁচ বছরের (১৮৮১—১৮৮৬) নিবিড় সান্নিধ্য, দীক্ষা ও গোপনীয় সাধনা ইসলামাবাদী (রহ.)—এর জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং তাঁর চিন্তা ও সাহিত্যকর্মে চিরস্থায়ী রূহানী দিকনির্দেশের আলোকরশ্মি হয়ে বিরাজমান।
জ্ঞানের বিস্তার:
হযরত কাজী আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন একাধিক জ্ঞানের দরবেশ—মুফাসসিরে কুরআন, শায়খুল হাদিস, ফকীহ ও তরিকতের পীর, পাশাপাশি বহু ভাষার পারদর্শী। বাংলা, আরবি, ফারসি ও উর্দুতে তাঁর পাণ্ডিত্যের দীপ্তি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইলমের তৃষ্ণা তাঁকে টেনে নেয় এক আধ্যাত্মিক মহাসাগরে।
শিক্ষকতা ও প্রভাব:
সুদীর্ঘকাল তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মোহসিনীয়া মাদ্রাসা—য় শিক্ষকতা করেন। তাঁর পাঠদান শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, আত্মার প্রশিক্ষণ। ছাত্রদের মধ্যে বহু মহাজ্ঞানী, পীর ও আলেম জন্ম নেন। এজন্য তাঁকে ডাকত “আল—উস্তাজুল উলামা”—আলেমদের ওস্তাদ। তাঁর জ্ঞান দীপ্ত সূর্যের মতো, নীরবতা জিকিরে নিমগ্ন নদীর মতো। চট্টগ্রামের ধর্মীয় শিক্ষা ও তাসাউফ চেতনার মূল শাখাগুলো তাঁর হাতে সিঞ্চিত হয়েছে।
শিক্ষকতা ও আলেম তৈরির প্রেরণা:
আল্লামা ইসলামাবাদী (রহ.)—এর শিক্ষকতা ছিল কেবল পাঠদান নয়; এটি ছিল আত্মার জাগরণের এক সূক্ষ্ম শিল্প। তিনি ছিলেন তৎকালীন আলেম সমাজের বাতিঘর। তাঁর ছাত্ররা ছিলেন আলোকিত মন—যারা পরবর্তীতে সমগ্র বাংলার দ্বীন ও আধ্যাত্মিকতার প্রদীপ জ্বালাল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ১. ওয়াহেদিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (রহ.), ২. আল—আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হযরত শাহ আবদুল কাদির মাদানী ইসলামাবাদী (রহ.), ৩. মাওলানা শাহ নজির আহমদ (রহ.)—সাতকানিয়া, ৪. চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীরের পিতা মাওলানা মীর আনোয়ার হোসেন (রহ.), ৫. মাওলানা আবদুল মাজিদ শাহ (রহ.)—গারাংগিয়া দরবার, সাতকানিয়া। এই অসংখ্য আলেমের মধ্য দিয়ে তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে। এজন্যই তাঁকে সমকালীনরা ডাকতেন “উস্তাদুল উলামা”, আলেমদের আলোকপাথপ্রদর্শক।
সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তি:
আল্লামা ইসলামাবাদী (রহ.) কেবল একজন ফকিহ বা ইতিহাসবিদ ছিলেন না—তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরবেশ ও ভাষার শিল্পী। তাঁর লেখায় আরবি—ফারসি শব্দরস, বাংলা ছন্দ, ও আধ্যাত্মিক ভাব একত্রে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ “কধুরখীল”—শুধু কাব্য নয়, বরং আত্মার মানচিত্র। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর জন্মভূমিকে আখ্যা দিয়েছেন “আল্লাহভক্ত ফকিরদের পদচিহ্নে ধন্য এক ভূমি”।
তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ:
(ক) “হযরতের গুণকীর্তন”— যেখানে তিনি তাঁর পীর—মুরশিদদের ফয়েজ ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি কাব্যরূপে প্রকাশ করেছেন। (খ) “খান বাহাদুর মৌলভী হামিদুল্লাহ খাঁন”— সমাজ ও প্রশাসনিক ন্যায়ের প্রশস্তি। (গ) “ইসলামাবাদ”— ইসলামি সভ্যতা, মানবতা ও ঐক্যের কাব্যগাথা। তাঁর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল অথচ মরমি। কখনও সরল বাক্যে জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন, আবার কখনও প্রতীকী রূপে আত্মার দিকনির্দেশনা করেছেন। তিনি লিখেছেন— “জ্ঞান সেই বাতি, যাহা আত্মার অন্ধকারে আলোক ছড়ায়; যাহার দীপ্তি নেভে না—সে—ই আল্লাহর বন্ধু।” এই পঙ্ক্তিতেই যেন তাঁর সারা জীবনের দর্শন নিহিত—জ্ঞান মানে আলোকিত ইবাদত।
ফারসি ও আরবি ঐতিহ্যের ধারক:
আল্লামা ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন বাংলা অঞ্চলের ফারসি—আরবি সাহিত্য ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি— যেমন, আলাওলের অনূদিত “সপ্ত পয়কর” এবং “শিরি খোসর” কাব্যের প্রাচীন সংস্করণ। তিনি এসব পাণ্ডুলিপি কেবল সংরক্ষণই করেননি, বরং পাঠ ও অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে মরমি ও শব্দসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তাঁর লেখায় ফারসি শব্দ যেন আত্মার দোয়া হয়ে গলে পড়ত, আর আরবি ভাবপ্রকাশ পেত রূহের সৌন্দর্যে।
সাহিত্যিক উত্তরাধিকার:
তাঁর জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যপ্রেমের ধারা থেমে যায়নি তাঁর মৃত্যুর পরেও। তাঁর বোন জমিরুন্নেসা, যিনি বাংলা ভাষার প্রথম মুসলিম মহিলা কবি হিসেবে পরিচিত, ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক উত্তরসূরি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ “মানিওল বেদাদ” আজও জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত— যা প্রমাণ করে, ইসলামাবাদী পরিবারের কণ্ঠে সাহিত্য ও তাসাউফের ধারা আজও বেঁচে আছে।
আধ্যাত্মিক জীবন ও কারামত:
তিনি ছিলেন এক সরল, নীরব দরবেশ, যার দৃষ্টি হৃদয় নরম করে দিত। জবান সর্বক্ষণ দরুদে মুস্তফা—তে সিক্ত। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ শরিয়তের ছায়াতলে; কখনো এক কদমও বাইরে নয়। তাঁর অঞ্চলে ঢোল—তবলা বা হারমনিয়ামের আওয়াজ নিষিদ্ধ; শোনা যায়, যেদিন বাজাতো, সেই দিনই বৃষ্টি নামতো—লোকেরা বিশ্বাস করত, “এ আল্লাহর ওলির ইশারা।” ফরিয়াদ আল্লাহর দরবারে অগ্রাহ্য হত না। মুখভর্তি দাড়িতে হাসলে মনে হতো, যেন নূর ঝলমল করছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন দরবেশের পোশাকে, আলেমের বুদ্ধিতে, এবং সাধকের নীরবতায় মোড়া এক আলোকিত সত্তা।
আধ্যাত্মিক জীবন ও তাসাউফ দর্শন:
আল্লামা ইসলামাবাদী (রহ.)—এর জীবন ছিল জ্ঞানের সাধনা ও আত্মার পরিশুদ্ধির এক সমান্তরাল যাত্রা। তিনি বিশ্বাস করতেন— “জিকিরহীন জ্ঞান আত্মাহীন দেহের সমান।” রাতের গভীর নীরবতায় তিনি মসজিদের মেঝেতে বসে কুরআনের আয়াত নিয়ে ধ্যান করতেন, কাঁদতেন, আর লিখতেন। তাঁর লেখায় তাই জ্ঞানের পাশাপাশি জিকিরের সুর বাজে। তিনি ছিলেন এমন এক আলেম, যিনি ‘কলমের ইবাদত’ করতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ছিল বিস্তৃত—তিনি আত্মাকে দেখেছেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, এবং আল্লাহর নূরকে সকল সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে।
রূহানিয় উত্তরাধিকার ও আধ্যাত্মিক বন্ধন:
হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন এমন এক রূহানিয় সাধক, যাঁর পরিবারও আল্লাহভক্তি ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত ছিল। তাঁর বোন মহিলা কবি জমিরুন্নেছা ছিলেন অন্তরে কবি, স্বভাবে দরবেশা; তিনি তাঁর জীবনে আল্লাহভীতির মাধুর্যে সিক্ত এক জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। নিয়মিত তিনি বোয়ালখালী থেকে সাম্পানযোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে যেতেন—কিন্তু প্রতি সফরের আগে ইসলামাবাদী (রহ.)—এর অনুমতি নিতেন। তাঁর সেই জিয়ারতযাত্রা ছিল যেন প্রেমিক হৃদয়ের সফর—একজন রূহানিয় নারীর নীরব নিবেদন। ইসলামাবাদী (রহ.) তাঁর সন্তানদেরও একই তাসাউফী আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুর রশিদ (রহ.)—এর বিবাহ গাউছুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রহ.)—এর খলিফা মাওলানা কাজী আব্দুস সোবহান (রহ.)—এর কন্যার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন ইউনাইটেড মুসলিম হাই স্কুল (বোয়ালখালী)—এর ধমীর্য় শিক্ষক এবং একই সঙ্গে কাজী বাড়ি জামে মসজিদের ইমাম; অর্থাৎ শিক্ষা ও ইবাদতের দুটি স্তম্ভ একত্রে ধারণকারী এক রূহানিয় আলেম। মেজোপুত্র মাওলানা কাজী এ. টি. এম. এহায়া (রহ.)—এর বিবাহ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাওলাপুরী (রহ.)—এর জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, যিনি গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা ছিলেন। মাওলানা এহায়া দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও রাঙামাটি স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর জীবনও ছিল এক আলোকিত খিদমতের পথ—নীরব দান, নীরব সাধনা, নীরব দোয়ার জীবন। এইভাবে ইসলামাবাদী (রহ.)—এর পরিবার পরিণত হয়েছিল আলেম, সুফি ও শিক্ষাসেবক বংশে, যেখানে রক্তের ধারায় জ্ঞানের নূর ও আধ্যাত্মিকতার সুবাস প্রবাহিত ছিল।
ইসলামাবাদী (রহ.) ও মাইজভাণ্ডারী পরিবারের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও আত্মিক। ইসলামাবাদী (রহ.)—এর পুত্র মাওলানা কাজী এ টি এম এহায়ার সঙ্গে সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন মাইজভাণ্ডারীর ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিয়মিতই দুজনের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান—প্রদান হতো, যা কেবল সৌজন্যের সীমায় সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ছিল আধ্যাত্মিক ভালোবাসা, সাহিত্যিক রুচি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন। সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন মাইজভাণ্ডারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী জানান, সেই চিঠিগুলো ছিল অত্যন্ত কাব্যিক ও হৃদয়গ্রাহী—যেন দুই আলোকিত হৃদয়ের অনুভূতি সেখানে মিশে আছে।
শাহজাদা আছিফ সাহেবের এক স্বাক্ষাৎকারে মাওলা হুজুর (সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র সন্তান)—বর্ণনা করেছেন যে সংরক্ষিত সেই চিঠিগুলো চাইলে খুঁজে দেখা সম্ভব, যদিও নানা ব্যবস্থাগত কারণে তা তখন প্রদান সম্ভব হয়নি। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে ইসলামাবাদী (রহ.) ও মাইজভাণ্ডারী পরিবারের মধ্যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনের এক গভীর সূত্র বিদ্যমান ছিল, যা কেবল পারস্পরিক সৌজন্য বা সামাজিক সম্পর্কের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এটি ছিল জ্ঞানের নূর, তাসাউফী আদর্শ, এবং সাহিত্যিক ও হৃদয়সংগত বন্ধনের এক অনন্য নিদর্শন।
আলেমসমাজ ও পীর—মাশায়েখদের শ্রদ্ধা ও রূহানিয় সংযোগ:
হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (র.) ছিলেন চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আলেম সমাজ ও পীর—মাশায়েখগণের কাছে রূহানিয় প্রেরণার এক অনন্য কেন্দ্র। ইসলামি জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা—মাসায়েল, কিতাবাদি অধ্যয়ন ও তরিকতের দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বজন স্বীকৃত দিকনির্দেশক ছিলেন। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা ও শিক্ষাদানের কারণে সমকালীন পীর, আলেম ও দরবেশগণ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। বিশেষ করে হযরত শামসুল উলামা গোলাম সালামানী আব্বাসী ফুরফুরাবাভী (রহ.)—যাঁর নিবাস ও মাজার ভারতের ফুরফুরা শরীফে—সঙ্গে তাঁর গভীর রূহানিয় সম্পর্ক ছিল। গোলাম সালামানী আব্বাসী ফুরফুরাবাভীর সিলসিলার অনুসারীগণও এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে আজও হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদের মাজার শরীফে ছুটে যান, রূহানিয় বরকত, ফয়েজ ও তাজাল্লিয়াত লাভের জন্য। এই সিলসিলার মধ্যে সৈয়দ আব্দুল বারী (রহ.)—গোলাম সালামানী আব্বাসী ফুরফুরাবাভীর খলিফা এবং হাফেজ হামেদ হাসান আজমগড়ী (রহ.)—সৈয়দ আব্দুল বারীর খলিফা ছিলেন।
এছাড়া হালিশহর দরবারের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ হাফেজ মুনিরুদ্দীন নুরুল্লাহ (রহ.), মাওলানা নজির আহমদ, গারাংগিয়া দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল মজিদসহ সকল পীরানে তরিক্বতের বুযুর্গগণ তাঁর মাজার শরীফে এসে রূহানিয় ফয়েজ লাভের জন্য ভক্তি প্রদর্শন করেন। দুই মহান আলেম—হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (র.) ও শামসুল উলামা গোলাম সালামানী আব্বাসী ফুরফুরাবাভী (রহ.)—নিজেদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে যুগের আলোকবর্তিকা ছিলেন। তাঁদের পীর ছিলেন সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসি—বর্ধমানী (রহ.), যাঁর মাজার ভারতের মানিকতলায় অবস্থিত। তাঁদের শিক্ষা ও তরিকতীয় প্রভাবের কারণে আজও অনেকে তাঁর মাজারে ছুটে যান, রূহানিয় বরকত ও তাজাল্লিয়াত লাভের জন্য। এইভাবে, হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (র.) জীবদ্দশায় যেমন আলেম সমাজ ও পীর—মাশায়েখগণের জন্য দিকনির্দেশক ছিলেন, ওফাতের পরও তাঁর মাজার শরীফ হয়ে উঠেছে আধ্যাত্মিক জাগরণ ও প্রেরণার এক পবিত্র কেন্দ্র।
সমাজে প্রভাব:
তাঁর প্রভাবে চট্টগ্রাম, ফেনী, রামু ও চুনতীর বহু আলেম ও তরুণ কবি সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হন। তাঁর কাব্য এক সময় মাদরাসাগুলোতে “উচ্চ আরবি—ফারসি ছন্দ বিশ্লেষণ”—এর পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন—ইলম, সাহিত্য ও তাসাউফ আলাদা নয়; এগুলোই মানবিক উন্নতির তিন স্তম্ভ। তাঁর চিন্তার ধারা অনুসরণ করেছেন আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী (রহ.), আল্লামা আজিজুল হক (রহ.), ও আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল গফুর (রহ.) প্রমুখ।
ভূয়সী প্রশংসা:
ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আজিজুল হক আল—কাদেরী তাঁর রচিত ‘দিওয়ান—ই—আযিয’—এ হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবী (র.)—এর প্রশংসা অত্যন্ত মহৎভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “আলিমকুলের শিরমণি, গুণীদের আদর্শ, আলিমগণের ওস্তাদ, গুণীজনদের পূর্ণিমা চাঁদ, কামিলগণের মুকুট, যুগের পথপ্রদর্শক, যুগপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, কাশ্ফ ও কারামতের খনি, ফায়েয—বরকতের প্রস্রবণ, কামালাতের ধারক, চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর কধুরখীল নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ সাহেব।” এই প্রশংসা আমাদের সামনে তুলে ধরে আল্লামা ইসলামাবী (র.)—এর আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগুণের মহিমা। মাওলানা আজিজুল হক আল—কাদেরী আরও লিখেছেন: “শত স্বাগতম, শত মুবারকবাদ, শত ধন্যবাদ—পরিশুদ্ধ আত্মা বিশিষ্ট মাওলানা আবদুল মজিদকে।” তিনি নিশ্চিত করেছেন, যে তিনি মাদ্রাসা—ই—মোহসেনিয়ার শিক্ষক, এবং সেই সময়ের শত সহস্র আলিম তাঁর ছাত্র হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠান গৌরবময় হয়েছে।
আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবী (র.) ছিলেন কাশফ ও কারামতের ধারক, কামেল পীর, এবং তাঁর বুযুর্গী ও কর্মকাণ্ডের সীমা লিখন—যাত্রা অতিক্রম করেছে। তাঁর নূরানী রওজা শরীফ আজও বোয়ালখালীর কধুরখীলে অবস্থিত এবং বহু মানুষ তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হয়। হযরত মাওলানা আজিজুল হক আল—কাদেরী দোয়া করেছেন: “হে বিশ্বপ্রতিপালক! তাঁর মাজার শরীফকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুন। হে মহান রব! নবীকুল সর্দারের উচিলায় এই দো’আ কবুল করুন।” তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ তাঁর রচয়িতার নাম জানতে চায়, তবে জানুক, তিনি হলেন ‘শেরে বাংলা’, যা ওলীগণের অস্বীকারকারীদের জন্য শানিত তরবারি। এই প্রশংসা, দোয়া ও বর্ণনা আমাদের সামনে তুলে ধরে হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবী (র.)—এর আধ্যাত্মিক গুণাবলী, শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞানচর্চা ও মানবসেবা—সব মিলিয়ে যুগান্তকারী চরিত্রের পরিচয়।
ইলমে—লাদুনীর অলৌকিক দীক্ষা:
মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)—যিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় এলাকার হযরত হাফেজ হামেদ হাসান (রহ.)—এর খলিফা ছিলেন। মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)—এর পুত্র মাওলানা হাবিবুর রহমান এক সাক্ষাতে শাহজাদা কে.বি.এম. আছিফকে বলেন— “আমার পিতা উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রওনা হওয়ার পূর্বে তিনি ইসলামাবাদী হুজুরের নিকট দোয়া নেওয়ার জন্য দরবারে উপস্থিত হন। তখন হুজুর কোনো কথা বলেননি; কেবল শান্তভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন—‘কাচারিতে বসে থাকো।’ সন্ধ্যার নীরব সময়ে হুজুর নিজেই আমার পিতাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—‘বাবা, কী বলতে চাও?’ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—‘হুজুর, আমি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় যাচ্ছি, কিন্তু আমার যাত্রার সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে।’ ইসলামাবাদী হুজুর তখন তাঁর সামনে বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ খুলে রাখলেন এবং প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন। পাঠ শেষে হুজুর গভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—‘তোমার আর হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই। যাও, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।” এই ছোট অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি প্রমাণ করে—হযরত ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন এমন এক নিভৃতচারী সুফি, যাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ইলমে—লাদুনী জ্ঞানের প্রভাবে শাগরেদদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আলোকিত হতো। তাঁর একটিমাত্র দৃষ্টিপাত, একটিমাত্র নির্দেশই ছিল আত্মার গভীরে পৌঁছানো এক অলৌকিক দীক্ষা। জাগতিক পাঠাগারে নয়, বরং হৃদয়ের নীরব প্রাঙ্গণে তিনি খুলে দিতেন জ্ঞানের দরজা। ইসলামাবাদী হুজুরের জীবন ও শিক্ষার এই রূপকথার মতো নিভৃতচারিতা আজও তরিক্বতপন্থী আলেম, সুফি ও মুরিদদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক আলোকধারা ছড়িয়ে দিচ্ছে—যেন এক অনন্ত জ্যোতির দীপশিখা, যা যুগে যুগে জ্ঞানের দরবেশদের পথপ্রদর্শক হয়ে জ্বলে থাকে।
রূহানিয় উত্তরাধিকার:
ইসলামাবাদী হযরতের বংশপরম্পরায় আধ্যাত্মিকতার এক অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়েছে। দুই—তিনজন ব্যক্তি মজজূব হালে জীবন অতিবাহিত করেছেন, যারা সংসার—পরিবারের ব্যস্ততা ত্যাগ করে পূর্ণতঃ আল্লাহভক্তি ও নীরব সাধনার মধ্যে মগ্ন ছিলেন। এই দুনিয়ার কোলাহল থেকে দূরে, তাঁরা ছিলেন রূহের নিখাদ পথিক, এক নিঃশব্দ দরবেশের মতো। ইসলামাবাদী হযরতের প্রপৌত্ররা—যারা আজও জীবিত—সেই আধ্যাত্মিক নীরবতার ধারাকে ধরে রেখেছেন। তবে কিছুদিন পূর্বে এ পরিবারের একজন সদস্য ইন্তিকাল করেছেন। এই সকল তথ্য ও ঘটনা প্রমাণ করে যে ইসলামাবাদী হযরতের পরিবার শুধু জ্ঞানী ও আলেমদের জন্মদাতা নয়, বরং এক তাসাউফী উত্তরাধিকারের ধারক, যেখানে রক্তের সঙ্গে আধ্যাত্মিক নূরও প্রবাহিত হয়।
মাজার শরীফ ও রূহানিয় উচিলায় আল্লাহর বরকত:
বায়তুল্লাহ, মদীনা শরীফ এবং বায়তুল মুকাদ্দেস হলো আল্লাহর নিদর্শন—রূহের তৃষ্ণা মেটানোর পবিত্র স্থান। এগুলোই মানুষের অন্তরকে আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত করে, যেখানে দৃষ্টিকোণ ও মননের গভীরতা আল্লাহর প্রেম ও নিকটতায় পরিণত হয়। হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদীর (র.) মাজার শরীফে ভক্ত ও অনুসারীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জিয়ারতের জন্য ছুটে আসে। এখানে দাঁড়িয়ে তারা অন্তরের গভীরতম স্থানে ফরিয়াদ জানিয়ে আল্লাহর দরবারে রূহানিয় বরকত ও তাজাল্লিয়াত লাভ করেন। আল্লাহর প্রিয় ওলীগণ, তাঁদের মাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, খানকা—সবই আধ্যাত্মিক নির্দেশক। কবরের পাশে দাঁড়ালে বান্দার হৃদয় মৃত্যুর স্মৃতিতে সতর্ক হয়, দুনিয়ার মোহমায়া থেকে মুক্তি পায় এবং রূহের গভীর আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর প্রতি মূর্ত হয়। এখানে আসা মানুষ নবীজির সুন্নাহ, ইসলামী জীবনব্যবস্থা এবং আল্লাহর প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নবীর সত্যিকারের উত্তরাধিকারী আলেম—ওলামা, যারা নায়েবে রাসুল হিসেবে মানুষের মধ্যে আল্লাহর জ্ঞান বিতরণ করেছেন, তাদের মাজারও জান্নাতের বাগানের অংশ। এভাবে, হযরত কাজী মাওলানা আবদুল মজিদ ইসলামাবাদীর (র.) মাজার শরীফ কেবল স্মৃতিস্তম্ভ নয়, বরং আধ্যাত্মিক যাত্রার এক পথপ্রদর্শক। এটি রূহানিয় উচিলার এক অনন্য কেন্দ্র, যেখানে বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী রসিক আনন্দ ও বরকত লাভ করে।
ইসলামাবাদীর ওরস শরিফ এক প্রাচীন ঐহিত্যের প্রতীক:
ইসলামাবাদী (রহ.)—যিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন—তাঁর পরিবার কেবল আধ্যাত্মিক সাধনায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তাঁরা সমাজের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এ প্রেক্ষাপটে আমি (লেখক) সম্প্রতি ৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালের একটি ওরসের দাওয়াতপত্রের মূল কপি হাতে পেয়েছি। দাওয়াতপত্রে বিনীতভাবে লেখা আছে—“বিনীত—তৎ অধম পুত্রগণ।” পত্রটির ভাষা ছিল অত্যন্ত মার্জিত, কাব্যিক ও ছন্দময়; প্রতিটি শব্দে জড়ানো ছিল অন্তরের বিনম্রতা ও আধ্যাত্মিক নিবেদনের সুর। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামাবাদী (রহ.)—এর সন্তানগণ কেবল নামের উত্তরাধিকারী নন, তাঁরা হৃদয়ের গভীর থেকে প্রকাশিত আধ্যাত্মিকতা, দরবেশি মনন ও ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠার উত্তরাধিকার বহন করতেন। এই দাওয়াতপত্র কেবল একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়—এটি ইসলামাবাদী পরিবারের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের এক জীবন্ত সাক্ষ্য, যা প্রমাণ করে যে ১৯৫০—এর দশকেও তাঁদের দরবেশি জীবনধারা, সামাজিক সংযোগ ও ধর্মীয় কার্যক্রম ছিল সুসংগঠিত, মর্যাদাপূর্ণ এবং সমাজে পরিচিত ও প্রভাবশালী।
উপসংহার:
আল্লামা শাহ কাজী আবদুল মজিদ ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন জ্ঞানের সাগরে সাঁতার কাটা এক দরবেশ। তাঁর কলমে জিকিরের সুর, তাঁর সাহিত্যে তাওহিদের গন্ধ, আর তাঁর জীবনে নূরের দীপ্তি। তিনি প্রমাণ করে গেছেন— আলেম হওয়া মানে কেবল জানা নয়, বরং জানা থেকে আলো ছড়ানো। তাঁর জীবন যেন তাসাউফের মাটিতে ফুটে থাকা এক ফুল, যার সুবাস আজও চট্টগ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
তথ্যসূত্র ও অবদান:
এই জীবনী রচনার ক্ষেত্রে ইসলামাবাদীর প্রপৌত্র খাজা বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ আছিফ আমাকে যথেষ্ট তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করেছেন। এছাড়া সাংবাদিক তাজুল এর “আলোকিত বোয়ালখালী” অনলাইন সংস্করণ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাকি বিষয়সমূহ ইতিহাস পর্যালোচনা ও প্রামাণ্য সূত্র অনুযায়ী যাচাই করা হয়েছে।
কলামিস্ট ও সাংবাদিক— কায়ছার উদ্দীন আল—মালেকী